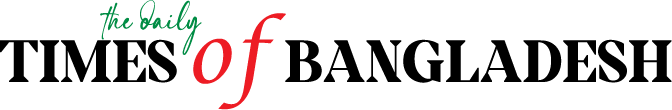২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শেখ হাসিনার একদলীয় শাসনের পতনের এক বছর হলো। এ পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ছাত্র ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক সৈকত আরিফের সঙ্গে টাইমস অব বাংলাদেশের তৌফিক হোসেন মবিন কথা বলেন। দেশের ছাত্র রাজনীতির বর্তমান অবস্থা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চলমান সংগ্রামসহ নানা বিষয়ে কথা বলেন আরিফ।
প্রশ্ন: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু শিক্ষার্থীর পক্ষ থেকে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধের দাবি উঠেছিল। এই দাবিকে আপনি কীভাবে দেখেন?
উত্তর: ছাত্ররাজনীতি বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি চালিকাশক্তি ছিল। ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ’৯০ এর স্বৈরাচার পতন সবকিছুর কেন্দ্রে ছিলেন ছাত্ররা। এরশাদ সরকার ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করতে চেয়েছিল, কিন্তু ব্যর্থ হয়েছিল। সেই ছাত্ররাই তাকে সরিয়ে দেন।
১৯৯০ সালের পর থেকে ছাত্ররাজনীতিকে পদ্ধতিগতভাবে দুর্নীতিপরায়ণ, সহিংস দেখানোর চেষ্টা হয়েছে। শাসকদলের ছাত্রসংগঠনের অপকর্মকে সামনে এনে পুরো ছাত্ররাজনীতিকে কলুষিত বলে প্রমাণ করার চেষ্টা চলে।
জুলাই আন্দোলনের সময় হঠাৎ করে কিছু মানুষ ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবি তোলে। অথচ ছাত্র নেতৃত্বাধীন সংগঠনগুলোর সঙ্গে কোনো আলোচনাই হয়নি। আমরা মনে করি, এটি আকস্মিক ছিল না, বরং একটি সুপরিকল্পিত রাজনৈতিক কৌশল ছিল। যেখানে আগে নিষিদ্ধ হয়ে যাওয়া কিছু সংগঠন (আন্ডারগ্রাউন্ড সংগঠন) আবার বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে আসতে চেয়েছিল।
প্রশ্ন: ‘আন্ডারগ্রাউন্ড সংগঠন’ বলতে আপনি কী বোঝাচ্ছেন?
উত্তর: ফ্যাসিবাদী সরকার পতনের পর হঠাৎ করে কিছু অচেনা মুখ ছাত্রনেতা হিসেবে আবির্ভূত হয়। অনেকেই ছিল ছাত্রশিবিরের সাবেক সদস্য। তারা তাদের পরিচয় গোপন রেখেই কখনো ছাত্রলীগের মিছিলে, আবার কখনো স্বতন্ত্র আন্দোলনে অংশ নেয়।
অভ্যুত্থানের পরে তারাই ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধের দাবি জোরালো করে তোলে, পরিচয় গোপন রেখেই। তাই আমরা এদের ‘আন্ডারগ্রাউন্ড’ বলি। তিতুমীর কলেজের একটি সাম্প্রতিক ঘটনা থেকেও এটি প্রমাণিত। এই বিভাজনমূলক দাবির মাধ্যমে তারা ছাত্র রাজনীতির কাঙ্ক্ষিত রূপান্তরকে আটকে দেয়।
প্রশ্ন: ছাত্র সংসদ নির্বাচন কি ছাত্ররাজনীতির মান উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে?
উত্তর: অবশ্যই। নির্বাচন থাকলে শিক্ষার্থীরা প্রকৃত নেতাকে বেছে নেওয়ার সুযোগ পান। অতীতেও দেখা গেছে, সবচেয়ে সহিংস সংগঠনও ভোটের মুখে পড়লে কিছুটা সংযত হতো। কিন্তু এখন যেহেতু নির্বাচন হয় না, নেতৃত্ব নির্ভর করে সিনিয়র নেতাদের খুশি করার ওপর। এতে নতজানু সংস্কৃতি তৈরি হয়, সহিংসতাও বাড়ে। নিয়মিত নির্বাচন থাকলে নেতৃত্ব ছাত্রসেবামূলক কর্মকাণ্ডে মনোযোগী হতো।
প্রশ্ন: তাহলে জুলাই আন্দোলনে ছাত্র সংগঠনগুলো সরাসরি অংশ নেয়নি কেন?
উত্তর: আন্দোলনটা কোটা সংস্কার নিয়ে শুরু হয়েছিল। এটি তৎক্ষণাৎ রাজনৈতিক বিদ্রোহ ছিল না। যেসব ছাত্র সংগঠন ফ্যাসিবাদবিরোধী অবস্থানে ছিল, তারা চিন্তা করেছিল, যদি তারা সরাসরি অংশ নেয়, তাহলে সরকার আন্দোলনটিকে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র হিসেবে প্রমাণ করার চেষ্টা করবে। তাই তারা নেপথ্যে থেকে সহায়তা করেছে—আশ্রয় দিয়েছে, সংগঠিত করেছে। ১৫ জুলাইয়ের দমন অভিযানের পর থেকে অনেকেই সামনে আসে।
প্রশ্ন: শেখ হাসিনার পতনের পর কি ফ্যাসিবাদ শেষ? নাকি আবার ফিরে আসতে পারে?
উত্তর: ফ্যাসিবাদ একদিনে তৈরি হয়নি। এটা তৈরি হয়েছে বিভাজনের মাধ্যমে। ২০১৪ সালের একতরফা নির্বাচনের পর রাজনীতিতে বিশ্বাস ও ঐক্য হারিয়ে যায়। হাসিনা সেই বিভাজনকে ব্যবহার করেছেন। ২০২৩ সালে গঠিত ‘ফ্যাসিবাদবিরোধী ছাত্র ঐক্য’ সেই বিভাজন ভেঙে দিয়েছিল।
কিন্তু ফ্যাসিবাদ শুধু কোনো সরকার ছিল না। এটি ছিল একটি কাঠামো—একটি বৈষম্যমূলক অর্থনীতি, একটি শ্রেণিভিত্তিক সংস্কৃতি। তাই শুধু সরকারের পতন যথেষ্ট নয়। যদি আমরা বৈষম্য ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে পরিবর্তন না আনতে পারি। তাহলে ফ্যাসিবাদ আবার ফিরে আসবে।
প্রশ্ন: উত্থানের পর ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে ঐক্য কেমন ছিল?
উত্তর: শুরুতে ঐক্য ছিল। এমনকি যখন ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধের দাবি উঠল, আমরা প্রকাশ্যে কিছু বলিনি। এর মূল কারণ ছিল ঐক্য ধরে রাখা। ৮ আগস্ট যখন অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়, আমরা ১২ আগস্ট বৈঠক করি। তখনই বলেছিলাম, ঐক্য ধরে রাখতে হবে। ‘বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন’ প্ল্যাটফর্মটা সবাই মিলে চালাতে হবে। কিন্তু কিছুদিন পর কিছু সংগঠনের নেতা এ গণঅভ্যুত্থানকে নিজস্ব সংগঠনের কৃতিত্ব হিসেবে দেখাতে শুরু করে। কেউ কেউ বলে, আন্দোলনের কৃতিত্ব শুধু তাদের। আবার শিবিরপন্থীরা বলে, পুরো আন্দোলন তাদের জন্যই হয়েছে। আমরা চেয়েছিলাম সবাই মিলে একটি অভিন্ন লক্ষ্য নির্ধারণ করতে। কিন্তু কেউ কেউ নিজেদের মতাদর্শকেই একমাত্র লক্ষ্য বানিয়ে ফেলে। এর ফলে ঐক্য ভেঙে যায়।
প্রশ্ন: জাতীয় রাজনীতিতে ছাত্র সংগঠনগুলো কী ভূমিকা রাখতে পারে?
উত্তর: আমাদের দেশের বেশিরভাগ জাতীয় নেতা ছাত্ররাজনীতি থেকেই উঠে এসেছে। এটা যেমন ছাত্র রাজনীতির শক্তি দেখায়, তেমনি একটি সমস্যা দেখায়—কৃষক-শ্রমিকদের নেতৃত্বে যাওয়ার পথ বন্ধ। জুলাই উত্থানে সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিরোধ এসেছিল বেসরকারি বা শ্রমজীবী এলাকাগুলো থেকে—বসিলা, আশুলিয়া, যাত্রাবাড়ী, উত্তরা ও দক্ষিণখান।
কিন্তু কোনো শ্রমিক নেতা আন্দোলনের প্রধান মুখ হতে পারেননি। কারণ, আমাদের সিস্টেম তাদের সেই সুযোগ দেয় না। এটা শুধু বৈষম্য নয়—এটা শ্রেণি ঘৃণা। একটি মেয়ের মরদেহ পাওয়া গিয়েছিল আন্দোলনের সময়। সবাই ভেবেছিল, তিনি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির ছাত্রী। তাই বিষয়টা ভাইরাল হয়। পরে জানা যায়, তিনি গার্মেন্টস কর্মী। তখন বিষয়টা সোশাল মিডিয়া থেকে একদম হারিয়ে যায়। এটাই প্রমাণ করে. আমরা শ্রমজীবী মানুষকে কতটা অবহেলা করি।
প্রশ্ন: তাহলে ছাত্ররাজনীতি থেকে জাতীয় নেতৃত্ব উঠে আসা কি ভালো না খারাপ?
উত্তর: শুধু ছাত্ররাই যদি নেতৃত্ব দেয়, তাহলে সেটা খারাপ। গণতন্ত্র মানে সব শ্রেণির কণ্ঠস্বর—ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক—সবার অংশগ্রহণ। ছাত্ররাজনীতি এখন এতটা আধিপত্য বিস্তার করছে। কারণ, অন্যদের সুযোগ নেই। এটা না পাল্টালে প্রকৃত গণতন্ত্র হবে না।
প্রশ্ন: ছাত্র ঐক্য পরিষদের অর্জন কতটা সফল?
উত্তর: রাজনৈতিকভাবে আমরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছি—সুন্দরবন রক্ষা, নিরাপদ সড়ক, কোটা সংস্কার এবং সর্বশেষ ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলন। আমাদের কমরেড জুলফিকার আহমেদ শাকিল আন্দোলনে শহীদ হন। আরও অনেক আহত হন। আমরা সম্মুখসারিতেই ছিলাম। এখন সংগঠনগতভাবে ধীরে হলেও এগিয়ে যাচ্ছি।
প্রশ্ন: ছাত্র সংসদ নির্বাচন হলে কী পরিকল্পনা রয়েছে?
উত্তর: আমরা চাই আদর্শভিত্তিক ছাত্র রাজনীতি হোক, পেশিশক্তিনির্ভর নয়।গণঅভ্যুত্থানের পর আমরা প্রস্তাব দিয়েছিলাম—সব সংগঠন মিলে কিছু নিয়ম লিখিতভাবে মানবে। যেমন-পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষ নয়, সহিংসতার বদলে বিতর্ক হবে। প্রথমে সেটা বাস্তবায়ন হয়নি, কিন্তু আমরা এখনো চেষ্টা করছি।
প্রশ্ন: অন্তর্বর্তী সরকার ছাত্ররাজনীতিকে কীভাবে দেখছে?
উত্তর: কোনো সরকারই ছাত্ররাজনীতি পছন্দ করে না। কারণ, ছাত্ররা সত্য কথা বলেন। এই সরকারও তার ব্যতিক্রম নয়। ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধের পরিকল্পনা এদের কেউ কেউ চালিয়ে গিয়েছে। আমরা সবাই যখন এর বিরোধিতা করেছি, তখনো সরকারের মনোভাব বদলায়নি।
প্রশ্ন: তাদের নিষিদ্ধের চেষ্টার কিছু উদাহরণ দিতে পারেন?
উত্তর: গণঅভ্যুত্থানের পর ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়। কিন্তু কোনো উপদেষ্টা, এমনকি যারা নিজেরাও একসময় ছাত্রনেতা ছিলেন, স্পষ্টভাবে কিছু বলেননি। শুধু নাহিদ ইসলাম হালকা মন্তব্য করেছিলেন। কেন? হয়তো তারা ক্ষমতা হারাতে চাননি, অথবা যারা পেছন থেকে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, তাদের বিরাগভাজন হতে চাননি। এই নীরবতাই ‘ব্যানড’ রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের প্রচেষ্টাকে সাহায্য করেছে।
এরশাদ বা আগের তত্ত্বাবধায়ক সরকারগুলোর মতোই এই সরকারও ছাত্ররাজনীতিকে নিষিদ্ধ করতে চায়। কারণ, তারা জানে ছাত্ররা সব বদলে দিতে পারেন। বর্তমান প্রধান উপদেষ্টা নিজেও আগের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় ছাত্ররাজনীতির বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন।