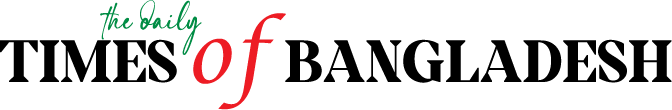বাংলাদেশের রাজনীতিতে ‘সংস্কার’ শব্দটির যেন এক অদ্ভুত চক্রবৃত্তি রয়েছে। নির্দিষ্ট সময় পর পর দেশের শাসন ব্যবস্থায় কিছু মুখ বদল হয়, প্রশাসনিক কিছু পরিবর্তন ঘটে, নতুন কিছু আইনি সংস্কারের কথা বলা হয়—আর একে নাম দেওয়া হয় ‘সংস্কার’।
অবশ্য শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগের টানা বছর পনেরর কর্তৃত্ববাদী সরকার ছিল এ হিসেবের বাইরে, তখন রাষ্ট্র থেকে শুরু করে প্রশাসনের ভিন্ন স্তরে মুখ ও মুখোশগুলো ছিল যেন অবকল একই।
তবে বাস্তবতা হলো, এসব সংস্কার যতটা রাজনৈতিক রূপ নেয়, তা নাগরিক চেতনায় ঠিক ততটা দাগ কাটতে পারে না।
সাম্প্রতিক সময়ের কথাই ধরা যাক। নোবেলজয়ী মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বধীন বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বলছে, প্রয়োজনীয় সংস্কার শেষে ডিসেম্বর অথবা জুনের মধ্যে নির্বাচন হবে। কিন্তু বিএনপিসহ কিছু রাজনৈতিক দল বলছে, নির্বাচন হতে হবে এ বছর ডিসেম্বরের মধ্যেই। এমন কি বৃহস্পতিবারই (১৭ এপ্রিল) বিএনপির শীর্ষ নেতা আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী সাংবাদিকদের এমনও বলেন, ‘এ বছর ডিসেম্বরের আগেও নির্বাচন হতে পারে।’
রাজনৈতিক দলগুলোর মতে, নির্বাচন বিলম্বিত হলে সেই অতি পরিচিত গা-ছাড়া মনোভাব রাজনীতিতে ফিরে আসবে। আর এ মনোভাব মানুষের কাছ থেকে নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে আরও দূরে সরিয়ে দেয়।
অন্যদিকে, নির্বাচনের আগে জাতীয় ঐকমত্যের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত ‘জুলাই চার্টারে’ বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক দল বিএনপি একমত হতে পারেনি। দলটি তাদের পূর্বঘোষিত ৩১ দফা সংস্কার-রূপরেখা থেকে সরছেই না। তবে অনুসন্ধান বলছে, এই ৩১ দফার মধ্যে যেসব সংস্কার দাবির সঙ্গে অন্যান্য রাজনৈতিক দল ও নাগরিক জোট একমত হবে, সেগুলো নিয়েই নির্বাচনের আগে আপাতত সংস্কারে ঐকমত্যে যেতে রাজি বিএনপি।
বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদের এলডি হলে বিএনপির প্রতিনিধি দলের সঙ্গে একমত্য কমিশনের বৈঠকে বিএনপি নেতা নজরুল ইসলাম খানের কথায় সেই ইঙ্গিতও স্পষ্ট। তিনি বলেছেন, ‘ঐকমত্যে জুলাই সনদ না হলেও বিএনপি’র ৩১-দফা সনদ আছে। সকল রাজনৈতিক দলের সাথে আলোচনা করে ৩১ দফা তৈরি করেছিল বিএনপি।’
এ পরিস্থিতিতে বিএনপির অবস্থান জটিল ও কৌশলগত। দলটি স্পষ্টভাবে জানিয়েছে, এ বছর ডিসেম্বরের পরে কোনো অবস্থাতেই জাতীয় নির্বাচন মেনে নেওয়া হবে না।
এর পেছনে রয়েছে দুটি বড় কারণ—প্রথমত, ভোটের আয়োজন বিলম্বিত হলে বর্তমান সরকারের ‘অন্তর্বর্তী’ চরিত্র প্রশ্নবিদ্ধ হবে। দ্বিতীয়ত, আগামী বছর জুন পর্যন্ত সময় দিলে প্রশাসনের পক্ষপাত এবং রাজনৈতিক প্রক্সি ব্যবস্থার আশঙ্কা বাড়ে।
বিএনপির অনেক নেতাকর্মীর ভয়, নির্বাচন যত বিলম্বিত হবে, দীর্ঘদিন ক্ষমতার বাইরে থাকা দলটির আবারও ক্ষমতায় যাওয়ার স্বপ্ন শেষ পর্যন্ত অধরাই থেকে যেতে পারে।
বিশ্লেষণ বলছে, বিএনপি তার অবস্থান দৃঢ় করতে এখন জামায়াতে ইসলামি ও অন্যান্য সমমনা দলগুলোকে আস্থায় আনার কৌশল নিচ্ছে, এমনকি তারা এরই মধ্যে তেমন সম্ভাবনাও কিছুটা তৈরী করতে পেরেছে।
যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনালের পর থেকে জামায়াত ও বিএনপির আনুষ্ঠানিক দূরত্ব থাকলেও, মাঠপর্যায়ে জামায়াতের সাংগঠনিক শক্তি এখনো গুরুত্বপূর্ণ—বিশেষ করে উত্তরাঞ্চল ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে। জানা গেছে, অন্তর্ভুক্তিমূলক ঐকমত্যে জামায়াতকে অন্তত ‘নীরব সমর্থক’ করে রাখার চেষ্টা করছে বিএনপি।
তবে এই কৌশলে জটিলতাও রয়েছে। ‘সংস্কার-ভিত্তিক ঐক্য’র প্রশ্নে জামাত এখনো দ্বিধান্বিত। দলটি যেমন নির্বাচনকালীন নিরপেক্ষ সরকার চায়, তেমনি তারা নির্বাচন কমিশনের পুনর্গঠন, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বাতিল এবং ধর্মীয় রাজনীতির স্বাধীনতা চায়। শেষোক্তটিতে আবার অন্যান্য ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলোর তীব্র আপত্তি রয়েছে।
জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের একজন সদস্য নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানিয়েছেন, বিএনপি এখন দুই রকম চাপের মুখে—একদিকে সংস্কারে নমনীয় হওয়ার চাপ, অন্যদিকে ধর্মীয়-রক্ষণশীল জোটকে আস্থায় রাখার চাপ। এই অবস্থান বজায় রাখা খুব একটা সহজ নয়।
এ পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠছে, বিএনপির ৩১ দফা সংস্কার দাবির কোনগুলো নিয়ে সর্বদলীয় ঐক্যমত্য সম্ভব? আবার বিএনপি যদি ডিসেম্বরে নির্বাচনই চায়, তবে তাদের সংস্কার প্রস্তাবে আপস না করে রাজনৈতিক ঐকমত্য গড়ে তোলা কীভাবে সম্ভব?
পর্যবেক্ষণ বলছে, এই পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো– জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন। ডিসেম্বরে নির্বাচন হলে, তা কি যথাযথভাবে সব দলের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হবে? আর না হলে, এটি কি আরেকটি সংকট তৈরি করবে?
জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ বলেছেন, ‘বিএনপি সুনির্দিষ্ট মতামত দিয়েছে, আমরা ভিন্ন মত নিয়ে আলোচনা করতে চাই। গণতান্ত্রিক সংগ্রামে বিএনপির ভূমিকা দেশের মানুষ অবগত। তাদের ভূমিকা জনগণের কাছে প্রশংসনীয়।’
কিন্তু প্রশ্ন হলো—সংস্কার আসলে কার জন্য? কাদের নিয়ে?
আজ পর্যন্ত যেসব তথাকথিত ‘সংস্কার’ হয়েছে, সেগুলোর কেন্দ্রবিন্দু ছিল প্রশাসন, নির্বাচন কমিশন, রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃত্ব ও বাহ্যিক কাঠামো। কিন্তু কখনো কি আমরা ভোটারদের মনোজগতে কোনো সংস্কার আনার চেষ্টা করেছি? আমাদের শিক্ষা, গণতান্ত্রিক অনুশীলন, নাগরিক দায়িত্ববোধ— এসব মৌলিক মানবিক জগতে কি সংস্কারের আলো পৌঁছেছে?
রাজনীতির মূল চালিকাশক্তি জনগণ। অথচ আজকের বাংলাদেশে জনগণ যেন শুধুই ‘ভোটার’, সিদ্ধান্তগ্রহণের অধিকার যেন তার নেই। একটি আদর্শ রাষ্ট্রে নির্বাচনে একজন প্রার্থীকে তার কাজ, নীতি ও দর্শনের উপর ভিত্তি করে মূল্যায়ন করা হয়। কিন্তু আমাদের বাস্তবতায় প্রার্থী নির্বাচনের প্রধান মানদণ্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে তার ‘মার্কা’, দলীয় পরিচয় এবং আর্থিক সক্ষমতা।
এই যে এখনো ভোটে জিততে হলে চাই অঢেল টাকা, দলীয় মনোনয়ন পেতে হলে দরকার পৃষ্ঠপোষকতা আর ‘প্যাকেজ ডিল’, সেখানে ভোটের বাজারে একজন আদর্শবান রাজনৈতিক কর্মী হয়ে ওঠেন উপহাসের পাত্র। তার জায়গা দখল করে নেন ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, বা ক্ষমতাধরদের সন্তান।
আর এমন প্রেক্ষাপটে একজন হিরো আলম বা দলছুট কেউ যেন হয়ে ওঠেন বিকল্প রাজনৈতিক চেতনার প্রতীক। এটি একদিকে যেমন রাজনৈতিক কাঠামোর ব্যর্থতা, তেমনি সমাজের সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের বহিঃপ্রকাশও।
রাজনীতি এখন আর জনসেবার প্ল্যাটফর্ম নয়, বরং এটি এক ধরণের বিনিয়োগ—যার ফলাফল পাঁচ বছরে হাতেনাতে নগদ প্রাপ্তি। মানুষ ভোট দেয়, জীবদ্দশায় নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন দেখে না। তারা আবার পাঁচ বছর পর ভোট দিতে যায়, তখনও চিন্তা করে না ‘আমি কী পেলাম’, বরং ভাবে ‘এইবার কোন প্রার্থী কম খারাপ’।
অন্যদিকে, সংস্কার-প্রক্রিয়া যতবার শুরু হয়, ততবারই মানুষ আশায় বুক বাঁধে। কিন্তু দিন গড়ালে দেখা যায়, সেই চেনা গল্পেরই পুনরাবৃত্তি হয়েছে—মুখ বদলেছে, পদ্ধতি বদলায়নি।
এক-এগারোর পর ২০০৭ সালে আমরা ‘ফখরুদ্দীন সংস্কার’র গল্প শুনেছি। ২০২৫ সালে দেখছি ‘ইউনূস সংস্কার’। কিন্তু এসব সংস্কারে ভোটার, নাগরিক, সাধারণ মানুষ—তাদের কী চেতনাগত সংস্কার হবে?
নির্বাচনী সংস্কার তখনই সার্থক হবে, যখন তা হবে সর্বস্তরের। সংস্কার প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক দলকে কেবল নিজেদের গণতন্ত্রের মুখপাত্র বলে আত্মতুষ্টিতে না ভুগে দায়িত্ব নিতে হবে তৃণমূলে মানুষের রাজনৈতিক সচেতনতা বাড়ানোর। আর
গণমাধ্যমের দায়িত্ব হবে সর্বত্র প্রশ্নবানে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, মোসাহেবির উৎসব আয়োজন নয়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রাজনীতি নিষিদ্ধ নয়, বরং সেখানে উত্সাহিত করা হবে সুস্থ রাজনৈতিক চর্চা।
এছাড়া নির্বাচন কমিশনকে হতে হবে গণতান্ত্রিক চেতনা প্রতিষ্ঠার প্রতিষ্ঠান হওয়া, এটি কেবল নির্বাচন পরিচালনার সংস্থা হবে না। সবচেয়ে বড় কথা, ভোটারকে ভাবতে হবে—তিনি শুধু একজন নামমাত্র ভোটদাতা নন, তিনি আসলে রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারক।
মৌলিক সংস্কারের প্রশ্নে যতদিন চেতনাগত সংস্কার না হয়, ততদিন যতোই ‘সংস্কার’র কথা বলি না কেন, সেটি হবে কেবলই ফাঁকা বুলি মাত্রা। আর তখন পাঁচ বছর পর পর বা নতুন কোনো কর্তৃত্ববাদী সরকার জাতির কাঁধে চেপে বসলে আরো লম্বা সময় পর ফিরে আসবে– সেই নতুন মুখ, আর পুরোনো ব্যর্থতা।