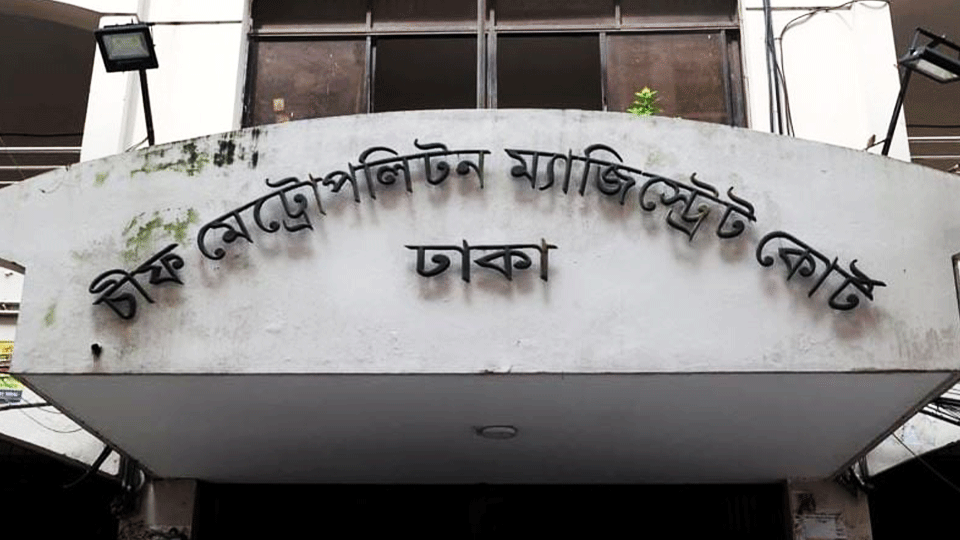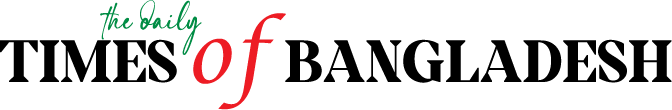আজ থেকে ১০ বছর আগে, আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ পরিমণ্ডলে উন্নয়নশীল বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির জন্য প্রশংসিত হচ্ছিল বাংলাদেশ। স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধি, বাড়তে থাকা রপ্তানি এবং যুবশক্তির বিশাল সম্ভাবনা বাংলাদেশকে অত্যন্ত সম্ভাবনাময় অর্থনীতি হিসেবে দাঁড় করিয়েছিল। কিন্তু ২০২৪ সালে, সেই একই দেশ অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে।
ব্যাংকিং সংকট, ডলারের অভাব এবং খেলাপি হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা– সব মিলিয়ে একটি হতাশার পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। এই পরিস্থিতিতে অর্থনৈতিক অবস্থা স্থিতিশীল করার দায়িত্ব নেয় অন্তর্বর্তী সরকার এবং অর্থনীদির নিম্নমুখী প্রবণতা থামিয়ে দেয়। এই সংকট মনে করিয়ে দেয় যে, শাসনব্যবস্থা দুর্বল হলে অর্থনৈতিক অগ্রগতি কতটা ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে।
এখন প্রশ্ন হলো, বাংলাদেশ কী এই পুনরুদ্ধারের মুহূর্তটি কাজে লাগিয়ে দীর্ঘমেয়াদী সমৃদ্ধির পথে চলতে পারবে? ২০৩৫ সালে বাংলাদেশ কোথায় দাঁড়াবে?
গত এক বছরে, অর্থনৈতিক খাতে আস্থা পুনরুদ্ধারে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। ব্যাংক খাতে সঙ্কট, বিনিময় হার অস্থিরতা এবং রিজার্ভের ঘাটতির মতো হুমকিগুলো নিয়ন্ত্রণে আনা গেছে। এক সময় যে আমদানিকারকরা ডলার সংগ্রহ করতে হিমশিম খেতেন, আজ তারা বাজারে ডলারের প্রবাহ দেখে আবার কাজ করতে পারছেন। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ পাঁচ-ছয় বিলিয়ন ডলার বেড়েছে।
ডলারের বিপরীতে টাকার মান প্রায় ১২২ টাকায় স্থিতিশীল রয়েছে এবং বেশ কয়েক বছর পর বাংলাদেশ ব্যাংক ডলার বিক্রির পরিবর্তে বাজার থেকে কিনতে সক্ষম হয়েছে। আন্তর্জাতিক অনেক অর্থদাতা যারা একসময় বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করেছিল, তারা আবার সম্পর্ক পুনরুদ্ধার করছেন। অনেকে ঋণ সীমাও বাড়াচ্ছেন। পরিশোধিত অর্থপ্রবাহ আবারও উদ্বৃত্তে ফিরেছে। এসব ঘটনা এক বছর আগেও অসম্ভব মনে হচ্ছিল, কিন্তু সেগুলোই এখন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাপ্রবাহ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।
তবে, অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার এখনো শেষ হয়নি। মুদ্রাস্ফীতি ৮ দশমিক ৫ শতাংশে আটকে আছে। যা ৪ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রার অনেক ওপরে। এই লক্ষ্যে পৌঁছতে হয়ত আরও এক বছর চেষ্টা করতে হবে। এ মুহূর্তে দুশ্চিন্তার চিন্তার বিষয় হলো ব্যাংকিং খাতের অবস্থা। বছরের পর বছর ধরে চলা প্রশাসনিক দুর্বলতা, কঠোর নিয়ন্ত্রণ না থাকা এবং প্রকাশ্য দুর্নীতির কারণে প্রতিষ্ঠানগুলো ক্ষতির প্রকৃত পরিমাণ গোপন করত এবং লোকসান হওয়ার পরেও লভ্যাংশ বিতরণ করত। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ঘোষিত ৯ শতাংশ নন-পারফর্মিং ঋণের সংখ্যা বাস্তবে আরও অনেক বেশি।
এখন কঠোর নীতিমালা কার্যকর হওয়ার পর, এটা স্পষ্ট হয়েছে সিস্টেমে থাকা ঋণ পোর্টফোলিওগুলোর এক চতুর্থাংশই খেলাপি এবং এ সংখ্যা আরও বেড়ে ৩০ শতাংশ পর্যন্ত হতে পারে। শুনতে খারাপ হলেও, এটিই সত্য যে এসব সংকট মোকাবেলা করতে হলে ব্যাংকিং খাতে সংস্কার করতেই হবে। এরই মধ্যে ১৫টি ব্যাংকে পরিচালনা পর্ষদ পুর্নগঠন করা হয়েছে এবং পুঁজির অভাবে থাকা প্রতিষ্ঠানগুলোকে লভ্যাংশ প্রদান থেকে বিরত রাখা হয়েছে। এই পদক্ষেপগুলো কষ্টকর, তবে এগুলোই সত্যিকারের সংস্কারের ভিত্তি তৈরি করছে।
এখানেই আসে সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয়, যেটি এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব না। বাংলাদেশ নিশ্চিতভাবেই আগামী ১০ বছরের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশের তালিকা থেকে ওপরের ধাপে উত্তীর্ণ হবে। তবে শুধুমাত্র এই উত্তরণ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নিশ্চিত করবে না। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো, বাংলাদেশ কি মধ্যম আয়ের দেশের নিম্ন স্তরের স্থবিরতা এড়াতে পারবে নাকি উচ্চ-মধ্যম আয়ের শ্রেণিতে উন্নীত হয়ে উন্নত অর্থনীতির দিকে এগিয়ে যেতে পারবে।
এই উত্তরটি নির্ভর করবে পরবর্তী দুইটি রাজনৈতিক সরকারের ওপর। যদি তারা স্থিতিশীল, সংস্কারপ্রবণ এবং গণতান্ত্রিক শাসনকে শক্তিশালী করার প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকে, তবে সফল পরিবর্তনের সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশি। কিন্তু যদি তারা পুরনো রেওয়াজে আটকে থাকে, দুর্নীতি সহ্য করে অথবা স্বৈরতান্ত্রিক প্রবণতা পুনরুজ্জীবিত হতে দেয়, তবে আশা পূর্ণ হবে না।
শাসনব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে। সাধারণ নাগরিকদের প্রতিদিনের জীবন সংগ্রামে এর প্রতিফলন দেখা যায়। যখন কেউ ঘুস না দিয়ে জাতীয় পরিচয়পত্রে ভুল সংশোধন করতে পারে না কিংবা ক্ষমতার জোর দেখিয়ে যখন কেউ একজন গ্রামবাসীকে তার জমি থেকে উচ্ছেদ করে, তখনই দেখা যায় নাগরিক অধিকারগুলো কতটা নাজুক অবস্থায় রয়েছে।
প্রশাসনিক কাজের অফিসগুলো, যেমন ভূমি রেকর্ড থেকে শুরু করে পুলিশ থানা ও কর বিভাগ কাজের অদক্ষতা ও দুর্নীতির জন্য বিখ্যাত। ফাইল হারিয়ে যায়, আবেদনগুলি বছরের পর বছর ধরে পড়ে থাকে এবং ঘুস না দিলে কোনো কাজই হয় না। এই যে সংস্কৃতি বছরের পর বছর ধরে গড়ে উঠেছে, তা প্রশাসন বা রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতি জনগণের আস্থা নষ্ট করে দিয়েছে। এসব প্রথাগত ব্যবস্থার সংস্কার না হলে, কোনো পরিসংখ্যানিক স্থিতিশীলতা বাস্তবে উন্নতি বয়ে আনবে না।
এরই মধ্যে এর ইতিবাচক পরিণতি সমাজে দৃশ্যমান। বাংলাদেশের শিক্ষিত তরুণদের একটি বাড়তি অংশ বিদেশে যাওয়ার সুযোগ খুঁজছেন। অভিভাবকরা স্পষ্টভাবেই বলছেন, তারা চান তাদের সন্তানরা বিদেশে বসবাস করুক। সন্তান দূরে চলে গেলেও তারা মনে করেন বিদেশে তাদের সন্তানের জন্য একটি নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ ভবিষ্যত রয়েছে।
২০৩৫ সালের মধ্যে এই অভিবাসনের সংখ্যা আরও বাড়বে এবং বাংলাদেশ থেকে হারিয়ে যাবে উজ্জল সব মেধারীরা। প্রকৃত উন্নয়ন কেবলমাত্র তখনই সম্ভব হবে যখন অভিভাবকরা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তাদের সন্তানদের বিদেশে লেখাপড়া শেষ করে দেশে ফিরে আসতে বলবেন। যখন দেশেই তারা কাজের মূল্য, সুযোগ এবং সম্মান পাবেন।
বিনিয়োগ আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ তৈরি করতে ব্যর্থ হয়েছে বাংলাদেশ। এই দেশে কেউ নতুন বিনিয়োগ করতে এলে প্রতি পদে পদে হয়রানির শিকার হতে হয়, প্রতি পদক্ষেপেই কেউ না কেউ ঘুসের দাবি নিয়ে আসে। রহস্যজনকভাবে ফাইলপত্র হারিয়ে যায় এবং এসবের জন্য কাউকে জবাবদিহিও করতে হয় না।
কিছু সংস্কার এখন চলছে। বাংলাদেশ ব্যাংক রয়েলটি, লভ্যাংশ এবং পুঁজি প্রত্যাবর্তনের জন্য পেমেন্ট প্রক্রিয়া সহজ করেছে। এগুলো এখন অনুমোদিত ব্যাংকের মাধ্যমে করা হয়। আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সম্পদ মূল্যায়ন পদ্ধতি গ্রহণের পরিকল্পনা চলছে, যাতে বিনিয়োগকারীরা আগে থেকেই জানতে পারেন তারা কীভাবে বৈধভাবে তাদের তহবিল ফেরত পাঠাতে পারবেন। এসব পদক্ষেপ অনিশ্চয়তা কমাচ্ছে এবং নতুন ধরনের উন্মুক্ততার সংকেত দিচ্ছে।
তবে এগুলো আরও বিস্তৃত করতে হবে। পদ্ধতিকে উদারীকরণ এবং স্বচ্ছতা অপরিহার্য। এগুলো না নিশ্চিত করা গেলে, বিনিয়োগকারীরা আসবেন না। যে শিল্পায়ন বাংলাদেশে অত্যন্ত প্রয়োজন, বিনিয়োগ ছাড়া তা অধরাই থাকবে। শিল্পায়ন এবং কর্মসংস্থান ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধির মেরুদণ্ড।
আনন্দের বিষয় হলো, নতুন বিনিয়োগের প্রতি আগ্রহের প্রথম চিহ্ন এরই মধ্যে দৃশ্যমান হয়েছে। গত এক বছরে বৈদেশিক সরাসরি বিনিয়োগ ২০ শতাংশ বেড়েছে। পোর্টফোলিও প্রবাহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। শেয়ারবাজারে নতুন প্রাণ ফিরেছে। এগুলো ছোট পদক্ষেপ হলেও, এগুলোর গুরুত্ব রয়েছে।
তবে শিল্পায়ন অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার ওপর নির্ভরশীল। ২০২৩ থেকে ২০২৫ সাল থেকে নেওয়া শিক্ষা হলো, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা একাই যথেষ্ট নয়। যখন অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা ব্যর্থ হয়, যখন রিজার্ভ কমে যায় এবং বিনিময় হার ধ্বংসের মুখে পড়ে তখন বিনিয়োগকারীরা পিছু হটে। এটি আর হতে দেওয়া যাবে না। অবশ্যই দায়িত্বশীলতার সঙ্গে অর্থের প্রবাহ পরিচালনা করতে হবে। এর মানে হলো, ঘাটতি পূরণের জন্য হুট করে অর্থ ছাপানো যাবে না। বরং, অর্থের প্রবাহ আসতে হবে পরিপূর্ণ অর্থপ্রবাহ উদ্বৃত্ত থেকে, বিদেশী পুঁজি প্রবাহ এবং আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীদের বন্ড কেনার মাধ্যমে। এই পন্থা মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি না করেই আর্থিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করবে।
ভাড়া আদায়ের রাজনীতিও এখন বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশের প্রধান বাণিজ্যিক কেন্দ্র চট্টগ্রাম বন্দর বারবার সুযোগসন্ধানী গোষ্ঠীগুলোর হাতে বন্দী হয়েছে যারা এটি ব্যবহার করে নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থ রক্ষা করতে চায়। এই আচরণ পুরো অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।
সমালোচকরা প্রায়ই বন্দর ব্যবস্থাপনায় বিদেশি সম্পৃক্ততার নিন্দা করেন, কিন্তু প্রায় প্রতিটি উন্নত অর্থনীতির দেশ তাদের বন্দরের দক্ষতা, প্রযুক্তি এবং আধুনিকীকরণের জন্য আন্তর্জাতিক অপারেটরদের ওপর নির্ভর করে। উদাহরণ হিসেবে সিঙ্গাপুর, দুবাই, রটারড্যাম এবং হংকংয়ের নাম বলা যায়।
যদি বাংলাদেশ এই কোম্পানিগুলোর সঙ্গে দশক বা তার বেশি সময়ের জন্য অংশীদারত্ব স্থাপন করে, তবে সেখান থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা শৈলী শেখা যেতে পারে এবং এরপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নেওয়া যেতে পারে। স্বল্পমেয়াদী রাজনৈতিক লাভের জন্য এই সুযোগ না নেওয়ার অর্থ হলো জাতীয় অগ্রগতির পথ রুখে দেওয়া।
আমলাতন্ত্র আরেকটি স্থায়ী চ্যালেঞ্জ হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। নাগরিকরা সরকারি অফিসগুলোতে হয়রানি এবং নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হন, অথচ এর জন্য দায়ী কর্মকর্তারা খুব কমই শাস্তির মুখোমুখি হন। জমি ব্যবস্থাপনা, শহর উন্নয়ন, পুলিশিং এবং কর প্রশাসন অদক্ষতায় পরিপূর্ণ। এমনকি প্রবল ইচ্ছাশক্তি থাকার পরেও অন্তবর্তীকালীন সরকারও এই বাধাগুলো অতিক্রম করতে পারেনি। ভবিষ্যতের নির্বাচিত সরকারকে এই সংস্কারগুলোর জন্য কঠোর চাপ প্রয়োগ করতে হবে, নাহলে প্রশাসনিক ব্যবস্থা এমন স্থবিরই থাকবে।
এখন ভবিষ্যতের আলোচনায় ফিরে আসি। ২০৩৫ সালের মধ্যে, বাংলাদেশ একটি রূপান্তরিত অর্থনীতির দেশে পরিণত হতে পারে, অথবা এমন একটি দেশ হতে পারে যা সেই পুরোনো দুর্বলতাগুলোর মধ্যেই আটকা পড়ে থাকবে। যদি শাসনব্যবস্থা শক্তিশালী হয়, যদি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো ঠিক মতো কাজ করে, যদি বিনিয়োগকে স্বাগত জানানো হয় এবং যদি শিল্পায়ন ত্বরান্বিত হয়, তবে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের ফাঁদ থেকে মুক্তি পেতে পারে এবং উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশগুলোর কাতারে দাঁড়াতে পারে। আর যদি তা না হয়, তবে দেশের উজ্জ্বলতম তরুণটা বিদেশে চলে যাবেন কাজের সন্ধানে, প্রতিষ্ঠানগুলোয় দক্ষ লোকের অভাব দেখা দেবে আর স্বপ্নগুলো অপূর্ণই রয়ে যাবে।
অর্থনৈতিক সূচকগুলো গুরুত্বপূর্ণ, তবে এর গভীর ভিত্তি হলো শাসনব্যবস্থা। যখন নাগরিকরা অনুভব করবে যে তাদের অধিকার সংরক্ষিত আছে, বিনিয়োগকারীরা আত্মবিশ্বাসী থাকবেন যে তারা শোষিত হবেন না এবং অভিভাবকরা বিশ্বাস করবেন যে তাদের সন্তানরা দেশে মর্যাদাপূর্ণভাবে বসবাস করতে পারবে, তখনই উন্নয়নের স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হবে। পরবর্তী এক দশকে নেওয়া সিদ্ধান্তগুলোই নির্ধারণ করবে যে ২০৩৫ এবং ২০৪০ সালে বাংলাদেশ একটি সফল গল্প হিসেবে উদযাপিত হবে, নাকি সুযোগ হারিয়ে ফেলার কারণে শোকার্ত হবে।
লেখক বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর