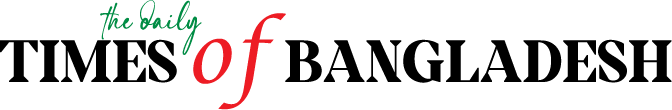জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর সাংবাদিক সমাজ ‘ভয়ভীতিহীন মুক্ত সাংবাদিকতা’ আশা করেছিল। কিন্তু দৃশ্যত পরিস্থিতির কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। অন্তর্বর্তী সরকারের সময়েও সাংবাদিকরা পেশাগত দায়িত্বপালন করতে গিয়ে শিকার হচ্ছেন হত্যা, মারপিট, হামলা ও হয়রানিমূলক মামলার। এসব বিষয়ে গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের প্রধান কামাল আহমেদ টাইমস অব বাংলাদেশের স্পেশাল অ্যাফেয়ার্স এডিটর এম আবুল কালাম আজাদকে দেওয়া বিশেষ সাক্ষাৎকারে বলেছেন খোলামেলা কথা।
‘কমিশন কোনো অবাস্তব সুপারিশ দেয়নি’ জানিয়ে জ্যেষ্ঠ এই সাংবাদিক বলেন, ‘বেশিরভাগ সুপারিশ শুধু সরকারি নির্দেশনা ও নীতিমালা হালনাগাদ করে বাস্তবায়ন করা সম্ভব ছিল।’ ‘কিন্তু সুপারিশমালা বাস্তবায়নে তথ্য মন্ত্রণালয় উল্টো পথে হাঁটছে,’ অভিযোগ করেন তিনি। ‘প্রতিহিংসার রাজনীতি হলে, জবাবদিহি ও আইনের শাসন না থাকলে সাংবাদিকরাও নিরাপদ থাকবে না,’ উল্লেখ করে তিনি ‘সাংবাদিকতা সুরক্ষা আইন’ প্রণয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। সাক্ষাৎকারটি নেওয়া হয় ৯ সেপ্টেম্বর।
টাইমস: জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর নতুন পটভূমিতে ‘ভয়ভীতিহীন মুক্ত সাংবাদিকতার’ বদলে, এখনো কেন বিপরীত চিত্র?
কামাল আহমেদ: আমাদের সবারই যে ধরনের উচ্চাশা ছিল, তা পূরণ হয়নি। কিন্তু এ ধরনের গণঅভ্যুত্থানের পর রাষ্ট্র ও সমাজে যে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি হওয়া স্বাভাবিক, সে কথা আমরা ভুলে বসেছিলাম। আমাদের প্রত্যাশা বাস্তবসম্মত ছিল না। একদিকে অন্তর্বর্তী সরকার যেমন বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও ছাত্রদের বিভিন্ন ধরনের শর্তসাপেক্ষ সমর্থনের ওপর নির্ভরশীল হওয়ার কারণে শক্ত হাতে কিছু করতে পারছে না; অন্যদিকে পুরোনো আমলাতন্ত্র এবং পুঁজিপতিরা আনুগত্য বদলের প্রতিযোগিতায় নেমে যার যার অবস্থান ঠিকই সংহত করে ফেলেছে। পাশাপাশি গত দেড় দশকে নানাভাবে নির্যাতিত ও বঞ্চিতদের প্রতিশোধ নেওয়ার তাড়না। এসবেরই পরিণতি হচ্ছে সরকারের সিদ্ধান্তহীনতা বা সিদ্ধান্ত গ্রহণে দীর্ঘসূত্রতা, বিভিন্ন মিডিয়া হাউসে অস্থিরতা ও চেয়ার দখল এবং কথিত মব বা দলবদ্ধ হামলা বা জেয়াফত আয়োজন বন্ধ করতে না পারা।

টাইমস: পেশাগত দায়িত্বপালন করতে গিয়ে এখনো সাংবাদিকরা শিকার হচ্ছেন হত্যা, মারপিট, হামলা ও হয়রানিমূলক মামলার। এজলাসে সাংবাদিকের ওপর হামলাও হয়েছে। সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে করণীয় কী?
কামাল আহমেদ: যে আইনজীবীরা সাংবাদিকের ওপর হামলা চালিয়েছেন তাদের রাজনৈতিক পরিচয় আছে। স্বৈরশাসনের আমলে তারা হয়তো কোনোভাবে বঞ্চিত হয়েছেন, নিজ না হলেও তার নেতা, সহযোগী বা আত্মীয়–স্বজন হয়রানির শিকার হয়েছে। সুতরাং তারা এখন সাবেক স্বৈরশাসকের সঙ্গে দূরতম সম্পর্কের অজুহাতেও অনেককে প্রতিশোধের লক্ষ্য বানাচ্ছেন। আর সাংবাদিকেরা এসব খবর প্রচার করলে যেহেতু সামাজিকভাবে বা রাজনৈতিকভাবে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন, সেহেতু খবর সংগ্রহে বাধা দিতে তারা হিংসাত্মক আচরণ করছেন। এখানে আদালতে দায়িত্বরত পুলিশ ব্যর্থ হয়েছে সম্ভবত আইনজীবীদের ভয়ে। আদালত কেন এই অঘটন আমলে নেননি, সেটা আদালতকেই বলতে হবে। আর আইনজীবীদের যে পেশাগত প্রতিষ্ঠানগুলো আছে, যেমন বার সমিতি – তাদের উচিত হবে নিজেদের পেশার মর্যাদা রক্ষায় ব্যবস্থা নেওয়া। নাহলে ভবিষ্যতেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে।
টাইমস: ঝুঁকিপূর্ণ পেশায় কাজ করেও অনেক সাংবাদিক যোগ্য বেতন-ভাতা পান না, চাকরির নিশ্চয়তাও নেই। এ অবস্থার উত্তরণ কি সম্ভব?
কামাল আহমেদ: সরাসরি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত সাংবাদিক ইউনিয়নের নেতাদের ধারণা বেতন–ভাতার একমাত্র সমাধান ওয়েজ বোর্ডে। আগে যে নেতারা দাপট দেখাতেন, সেই আওয়ামী সমর্থক ইউনিয়নের নেতারা সাংবাদিকদের বেলায় শ্রম আইন প্রয়োগের প্রসঙ্গ উঠলে শরম বোধ করতেন। তারা আলাদা গণমাধ্যমকর্মী আইন চেয়েছিলেন। অথচ, বাস্তবতা হচ্ছে, শ্রম আইন কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা হলে বেতন–ভাতা বকেয়া রাখা কিংবা কর্মক্ষেত্রে হয়রানি ও যখন–তখন চাকরিচ্যুতি বন্ধ করা সম্ভব। বিষয়টি শুধু ব্যাংক কর্মচারী কিংবা পোশাক শ্রমিকদের দিকে তাকালেই বোঝা যাবে। বকেয়া বেতন না দেওয়ায় তিনজন গার্মেন্টস মালিকের বিরুদ্ধে এখন আন্তর্জাতিক গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বা ইন্টারপোলের রেড নোটিশ জারি হয়েছে।
আর যে ওয়েজ বোর্ডের কথা বললাম – সেটি আদালতে আটকে আছে প্রায় পাঁচ বছর। সরকার সেখানে কোনো পক্ষ নয়। মালিকদের পক্ষ থেকে মামলা করা হয়েছে। সরকার কি কোনো নাগরিককে মামলা প্রত্যাহারের কথা বলতে পারে?
সুতরাং, মামলা যদি আরও পাঁচ বছর ঝুলে থাকে আরও পাঁচ বছর চলতে হবে পুরোনো বেতনে। অথচ, গত পাঁচ বছরে মূল্যস্ফীতি ঘটেছে বার্ষিক গড়ে ১০ শতাংশ হলেও মোট ৫০ শতাংশের বেশি। কমিশন থেকে তাই আমরা বলেছি, সরকারি কর্মকর্তাদের নবম গ্রেডের যে বেতন স্কেল সেটিকে সাংবাদিকদের ন্যূনতম বেতন হতে হবে। তারপর প্রতিবছর সরকারি হিসাবে যে মূল্যস্ফীতি সেই হারে বেতন বাড়াতে হবে। অন্যান্য পদগুলোর বেতন হার মালিক ও ইউনিয়নগুলো অথবা ব্যক্তিগত আলোচনাতেই নিষ্পত্তি হতে পারে। আর শ্রম আইন কঠোরভাবে কার্যকর করতে হবে। তাহলে সাংবাদিকদের দৈন্যদশার অবসান ঘটবে। ন্যূনতম বেতন নির্ধারণে আইনে কোনো সমস্যা আছে কি না –এমন প্রশ্ন উঠতে পারে। তবে এখানেও শ্রম আইন অনুসৃত হলে কোনো বাধা থাকার কথা নয়। ত্রিপক্ষীয় আলোচনায় বসে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ তো অন্য সব খাতেই ঘটে।

টাইমস: সাংবাদিকতা পেশার সুষ্ঠু বিকাশে গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের ছয় মাস আগে প্রতিবেদন জমা দিলেও এখনো এর সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন হয়নি। গুরুত্বপূর্ণ এসব সুপারিশ বাস্তবায়নে বাধা কোথায়?
কামাল আহমেদ: অনুমানের ভিত্তিতে কিছু বলা যাবে না। প্রশ্নটা সরকারের কাছে করা উচিত। তথ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপদেষ্টা অথবা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে সংস্কার কার্যক্রম সমন্বয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত সচিব ভালো জানবেন। আমি শুধু যেটুকু জানি সেটাই বলতে পারি। তথ্য মন্ত্রণালয়ের আমলারা সংস্কারের সুপারিশগুলো বাস্তবায়নের বিষয়ে অংশীজনদের মতামত ও সহযোগিতা না চেয়ে উল্টোপথে হাঁটছেন। আমরা ব্যর্থ ও অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়া প্রেস কাউন্সিলের বিলুপ্তি ঘটিয়ে নতুন প্রতিষ্ঠান তৈরি করতে বললাম। কিন্তু সেই প্রস্তাবিত জাতীয় গণমাধ্যম কমিশনের সুপারিশ উপেক্ষা করে তারা প্রেস কাউন্সিলের জন্য গত জানুয়ারিতে – অর্থাৎ কমিশন যখন কাজ করছিল, সেই সময়ে মালিক ও সম্পাদক পরিষদ যাদের মনোনয়ন দিয়েছিল, তাদের নাম দিয়ে মৃত্যুন্মুখ প্রেস কাউন্সিলকে পুনর্জীবন দিয়েছেন। তারা একই কাণ্ড করেছেন গণমাধ্যমকর্মী (চাকরির শর্তাবলি) আইন নিয়ে। ওই আইনের খসড়া বস্তার তলা থেকে বের করে এনে তারা মালিক, সম্পাদক ও ইউনিয়নগুলোর মতামত চেয়েছেন। সরকারি অর্থের অপচয় বন্ধের জন্য কমিশন যেখানে বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থাকে পুনর্গঠন ও বিটিভি–বেতারের সঙ্গে একীভূতকরণের জন্য বলেছে, সেখানে অনুমোদিত বাজেট ও লোকবলের বাইরে নতুন করে ৪৫ জনের নিয়োগ অনুমোদন করেছে। আগেই সেখানে অনুমোদিত লোকবলের চেয়ে এক–তৃতীয়াংশ জনবল বেশি ছিল। অথচ, বিটিভির ওপর মন্ত্রণালয়ের এমনই নিয়ন্ত্রণ যে তাদের একটি ভাঙা গাড়ি মেরামতের জন্য ৫০ হাজার টাকা খরচ করতে হলে সচিব থেকে শুরু করে ১৪ টেবিলে সেই ফাইলে অনুমোদন লাগবে।
টাইমস: গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের কোন কোন সুপারিশ ইতোমধ্যেই বাস্তবায়ন করা উচিত ছিল?
কামাল আহমেদ: কমিশন কোনো অবাস্তব সুপারিশ করেনি। বেশিরভাগ সুপারিশই শুধু সরকারি নির্দেশনা এবং নীতিমালা হালনাগাদ করার মাধ্যমেই বাস্তবায়ন সম্ভব। যেগুলোতে সময় লাগবে, সেগুলোও সরকার শুরু করতে পারতো, যাতে পরের সরকার তা পরিত্যাগ করলে তাকে গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা দিতে হতো। যেমন একই প্রতিষ্ঠানে বহুবিধ গণমাধ্যম প্লাটফর্মের মালিকানার কারণে যে প্রভাবক ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ ঘটেছে, সেটি ভেঙ্গে দিতে সরকার নির্দেশনা দিয়ে সময় বেঁধে দিতে পারতো। এর জন্য আইন করার প্রয়োজন পড়ত না। কেননা, লাইসেন্সগুলোও দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন নীতিমালার ভিত্তিতে। সাংবাদিকতা সুরক্ষা আইন এবং স্থায়ী গণমাধ্যম কমিশন গঠনের জন্যও সরকার অধ্যাদেশ জারি করতে পারে। এই দুটি আইন এবং কমিশন গঠন স্বাধীন সাংবাদিকতার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একইভাবে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বেতার–টিভির স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টিকে সরকার অগ্রাধিকার না দিয়ে বড়ধরনের ভুল করছে। রাজনৈতিক সরকার কাজটি করতে আগ্রহী হবে না এবং আমলারা তা করতে দেবে না। কেন দেবে না, সেকথা আমি আগেই বলেছি।

টাইমস: গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের সুপারিশগুলো বাস্তবায়নে করণীয় কী? বাস্তবায়ন হলে কি অবস্থার উন্নতি হতো?
কামাল আহমেদ: কোন সুপারিশ কীভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে, সেই পথ আমাদের প্রতিবেদনে বলে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং করণীয় নতুন করে বলার কিছু নেই। বাস্তবায়ন হলে সাংবাদিকদের এবং সংকটে থাকা গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলোর আর্থিক স্বাধীনতা ফিরতো এবং বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা সম্ভব হতো। ভুইফোঁড় প্রতিষ্ঠানগুলোর কথা অবশ্য আলাদা।
টাইমস: সাংবাদিকতায় এখন নিরাপত্তাহীনতা, নানান ধরনের হুমকি, আরও বেশি সেল্ফ সেন্সরশিপ রয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এ বিষয়ে আপনার মতামত কী?
কামাল আহমেদ: সেলফ–সেন্সরশিপের কারণ মূলত মব বা বিভিন্ন গোষ্ঠীর হুমকি। আবার এসব গোষ্ঠীর পেছনে আছে কিছু সোশ্যাল–মিডিয়ার পীর। সরকারের দিক থেকে কোনো হস্তক্ষেপ বা হুমকির ঘটনা ঘটেছে কি না তা বার্তাকক্ষগুলো যারা চালান, তারাই বলতে পারবেন। কোনো প্রতিবেদন বা মতামত কলামে ভুল বা বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রকাশ পেলে তা সংশোধনের জন্য সরকারের কেউ দৃষ্টি আকর্ষণ করলে সেটিকে হস্তক্ষেপ বলা কি যৌক্তিক হবে?
টাইমস: ফেব্রুয়ারির নির্বাচনকে ঘিরে আশঙ্কা করা হচ্ছে আগামী দিনে রাজনৈতিক সহিংসতা বাড়তে পারে। এক্ষেত্রে কি সাংবাদিকতা আরও বেশি কঠিন হয়ে পড়বে?
কামাল আহমেদ: রাজনৈতিক সহিংসতা বাড়লে সাংবাদিকদের জন্য যে ঝুঁকি বাড়বে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সমাজে এখন অসহিষ্ণুতা চরমে। সাংবাদিকতা সুরক্ষা আইন এ কারণেই জরুরি ছিল। প্রতিকারের ব্যবস্থা না থাকলে, বিচার হবে না জানলে অন্যায়কারীরা তো উৎসাহ পাবেই। আমাদের সব সময়েই স্মরণ রাখা দরকার মতপ্রকাশের স্বাধীনতা হচ্ছে, ততক্ষণ সবকিছু বলতে পারা যতক্ষণ না তা অন্যের ক্ষতির কারণ হয়। এখন প্রতিহিংসার রাজনীতি হলে, জবাবদিহি ও আইনের শাসন না থাকলে সাংবাদিকরাও নিরাপদ থাকবে না।