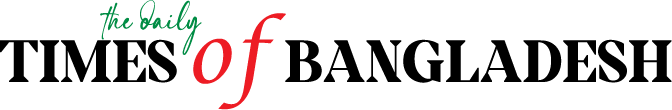অন্তর্বর্তী সরকারের সিদ্ধান্তহীনতায় থমকে গেছে পাচারের অর্থ উদ্ধারের প্রক্রিয়া। দায়িত্ব গ্রহণের ১৩ মাস পার হলেও সংশ্লিষ্টরা অর্থ উদ্ধারের জন্য ‘নতুন আইনের খসড়াই’ প্রস্তুত করতে পারেনি বলে জানা গেছে। কবে নাগাদ চূড়ান্ত হবে সেটিও জানা নেই কর্মকর্তাদের।
গত ১০ মার্চ প্রধান উপদেষ্টার সভাপতিত্বে ‘পাচারকৃত সম্পদ পুনরুদ্ধার, গৃহীত পদক্ষেপ ও চ্যালেঞ্জ’ শীর্ষক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক শেষে প্রেস সচিক শফিকুল আলম সংবাদ সম্মেলনে বলেছিলেন, ‘পাচার হওয়া এই টাকা কীভাবে ফেরত আনা যায়, সে বিষয়ে একটি বিশেষ আইন খুব শিগগির করা হবে। আগামী সপ্তাহের মধ্যে এ আইনটি দেখা যাবে।’
ওই ঘোষণার পর ২৫ সপ্তাহ পার হয়ে গেলেও দৃশ্যত নেই অগ্রগতি।
পাচারকৃত অর্থ উদ্ধার ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত টাস্কফোর্স কমিটির চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুর টাইমস অব বাংলাদেশকে বলেন, ‘তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের কারণে অর্থ উদ্ধারের প্রক্রিয়াটি “প্যারালাইসিসড” হয়ে যাচ্ছে। আমরা কী ছাড়বো, না ছাড়বো না। আমরা কী ধরবো, না ধরবো না। আমরা ফৌজদারিতে যাব না দেওয়ানি মামলায় যাব? সরকার হয়তো এই তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের কারণে কোন সিদ্ধান্ত দিতে পারবে না।’
বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাবেক মহাপরিচালক ড. মুস্তফা কে মুজেরী টাইমস অব বাংলাদেশকে বলেন, ‘অর্থ উদ্ধারের প্রক্রিয়া জরুরিভিত্তিতে শুরু করতে সরকার ব্যর্থ হয়েছে। এটিকে যতটা অগ্রাধিকার দেওয়া দরকার ছিল সেটি সরকার দেয়নি। আইন তৈরিতেই এক বছরের বেশি সময় পার হয়ে গেলে সন্দেহ চলেই আসে, আদৌ সরকার অর্থ উদ্ধারে কোনো অগ্রগতি অর্জন করতে পারবে কি না।’
বাংলাদেশ ব্যাংকের এই সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ বলেন, ‘পাচারকারীরা যত সময় পাবে তারা নিজেদের পাচারকৃত সম্পদ আরও বেশি সুরক্ষা দিতে সক্ষম হবে। অর্থ উদ্ধার আরও দুষ্কর হয়ে পড়বে।’
অন্তর্বর্তী সরকারের হিসাবে, বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের পনেরো বছরের শাসনামলে ৭৫০০ থেকে ১০ হাজার কোটি ডলার পাচার হয়েছে।
অর্থ মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, নতুন আইনে দেওয়ানী মামলার বিধান রাখা এবং সমঝোতার মাধ্যমে পাচারের টাকা ফেরত আনার সুযোগের প্রশ্নে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারছে না সরকার। যদিও শ্রীলঙ্কা, ভারত ও পাকিস্তানের আইনে এমন সুযোগ থাকায় সাফল্য এসেছে।
বিদ্যমান ‘মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে’ পাচারের অপরাধে শুধু ফৌজদারি মামলা ও শাস্তির বিধান রয়েছে। ২০১২ সালের জানুয়ারি থেকে কার্যকরের পর এই আইনের অধীনে অর্থ উদ্ধারের কোন তথ্য নেই।
খসড়া তৈরির সঙ্গে যুক্ত থাকা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মো. আজিমুদ্দিন বিশ্বাস টাইমস অব বাংলাদেশকে বলেন, ‘নতুন মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন নিয়ে অংশীজনদের মতামত নেওয়া হয়েছে যেখানে বিভিন্ন প্রস্তাব এসেছে। তবে এখনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি।’
এদিকে ভারত ও শ্রীলঙ্কায় একটি সংস্থার অধীনে অর্থ উদ্ধারের প্রক্রিয়া পরিচালিত হলেও বাংলাদেশে কাজ করছে আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা বিএফআইইউ, অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি) ও দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। সমন্বয়হীনতা রোধে কার্যক্রমটি একটি সংস্থার অধীনে আনার বিষয়েও সরকারের চিন্তা নেই বলে জানা গেছে।
অতিরিক্ত সচিব আজিমুদ্দিন বিশ্বাস বলেন, ‘অর্থ পাচার রোধ ও এর উদ্ধার প্রক্রিয়া একক সংস্থার অধীনে নিয়ে আসার বিষয়ে বৈঠকগুলোতে কোনও আলোচনা হয়নি।’ অপরাধের ধরন অনুযায়ী যাদের কাজ তারা করবে, সমস্যা নেই বলে উল্লেখ করেন তিনি।
খসড়া তৈরির কাজ শেষ হতে কতদিন লাগবে জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘এটি আসলে আমাদের জানা নেই। তবে আইনটি সরকারের অগ্রাধিকার বিবেচনায় রয়েছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব করা হবে।’
নাম প্রকাশ না করার শর্তে অর্থ মন্ত্রণালয়ের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, ‘আইনে দেওয়ানি মামলার ও সমঝোতার ভিত্তিতে অর্থ ফেরত আনার বিধান থাকছে কি না সেগুলো এখনো মীমাংসা হয়নি।’
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব নাজমা মোবারেক টাইমস অব বাংলাদেশকে বলেন, ‘খসড়ার তৈরির কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। এটর্নি জেনারেলের কাছে মতামত চাওয়া হয়েছে।’
দক্ষিণ এশিয়ার অভিজ্ঞতা কাজে লাগাচ্ছেনা বাংলাদেশ:
শ্রীলঙ্কা ও ভারত আইনগত সংস্কারের মাধ্যমে অর্থ উদ্ধারে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখালেও এখনো প্রস্তুতি ও নীতিগত পরিকল্পনার পর্যায়ে রয়ে গেছে বাংলাদেশ। পাচারকৃত অর্থ ফেরাতে পাকিস্তান সাফল্য দেখাতে পারলেও উল্লেখ করার মতো অর্জন নেই বাংলাদেশের।
চলতি বছরের এপ্রিলে শ্রীলঙ্কা ‘প্রসিডস অব ক্রাইম এক্ট ২০২৫’ প্রণয়ন করেছে যাতে আদালতের রায় ছাড়াই অবৈধ সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে অর্থ উদ্ধারে নিয়োজিত দেশটির একক সংস্থাকে। পাশাপাশি এই আইনে দেওয়ানি মামলা ও সমঝোতার ভিত্তিতে অর্থ ফেরত আনার বিধান যুক্ত হয়েছে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল শ্রীলঙ্কা এটিকে ল্যান্ডমার্ক আইন হিসেবে অভিহিত করেছে যার মাধ্যমে অর্থ উদ্ধার প্রক্রিয়া বেগবান হয়েছে।
ভারতে ২০১৮ সাল থেকে এমন আইন রয়েছে যার মাধ্যমে বেশ সাফল্য এসেছে। প্রেভেনশন অব মানি লন্ডারিং এ্যক্ট (পিএমএলএ) ও এফইও এ্যক্ট ব্যবহার করে দেশটির এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) সম্প্রতি বড় অঙ্কের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করেছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে দেশটি ২৩ হাজার কোটি রুপি উদ্ধার করতে পেরেছে এবং আদালতে অনুমতি নিয়ে ১৫,২৬১ কোটি রুপি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ও ব্যাংকগুলোর কাছে ফিরিয়ে দিয়েছে।
এদিকে অর্থ উদ্ধারে সাফল্য পেয়েছে পাকিস্তানও। দেশটি ২০১৯ সালে যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল ক্রাইম এজেন্সির সঙ্গে সিভিল সেটেলমেন্টের মাধ্যমে ১৯ কোটি পাউন্ড দেশে ফেরাতে সক্ষম হয়েছিল।
পাচারের অর্থ উদ্ধারে আন্তর্জাতিক সহায়তা গ্রহণ ও প্রদানে বাংলাদেশে ২০১২ সালের মিউচ্যুয়াল লিগ্যাল এসিস্ট্যান্ট এ্যক্ট থাকলেও এখনো কার্যকর অ-দণ্ডভিত্তিক (এনসিবি) সম্পদ বাজেয়াপ্তি আইন নেই। এখানে বিএফআইইউ প্রাথমিক তদন্ত করে সিআইডি ও দুদকের কাছে নথি প্রেরণ করে। এই সংস্থা দুটি আদালতের কাছে সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার অনুরোধ করতে পারে যা কার্যকর করতে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হয়।
বিশ্লেষকরা বলছেন, বাংলাদেশ মূলত তিনটি ক্ষেত্রে প্রতিবেশীদের চেয়ে পিছিয়ে আছে। আইনী কাঠামো না থাকায় দ্রুত সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা যায় না। অর্থ উদ্ধারে একক কর্তৃপক্ষ না থাকায় বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয় জটিলতা হয়। সমঝোতার ভিত্তিতে কিংবা দেওয়ানি মামলার মাধ্যমে অর্থ উদ্ধারের সুযোগসম্বলিত আইন না থাকায় অর্থ উদ্ধার সম্ভব হচ্ছে না। কারণ, ফৌজদারি বা ক্রিমিনাল মামলা প্রমাণ করে শাস্তি নিশ্চিত করার মতো সক্ষমতা বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠানগুলোর নেই।
প্রবীণ অর্থনীতিবিদ ও গভর্নর আহসান এইচ মনসুর বলেন, পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে দেওয়ানী মামলার মাধ্যমে বেশিরভাগ অর্থপাচার মামলার সমাধান হয়। কিন্তু আমাদের দেশে আইন করা হয়েছে ফৌজদারি বিষয়গুলো প্রাধান্য দিয়ে। যে কারণে আমাদের দেশে চূড়ান্তভাবে কোন বিচার হয় না। ফৌজদারি আইনে কাউকে আটকানোও যায় না। কারণ ফৌজদারি অপরাধ প্রমাণের সামর্থ আমাদের কর্মকর্তাদের নেই। সব মিলিয়ে আমার কাছে মনে হয় যে, অনেকগুলো ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত আমাদেরকে দেওয়ানী মামলায় যেতে হবে।
পাচারকৃত অর্থ উদ্ধারে অগ্রগতি জানতে চাইলে এ সংক্রান্ত টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান মনসুর বলেন, ‘কিছু অগ্রগতি হয়েছে। আবার একটু মন্থরও হয়েছে। কিছু মৌলিক সিদ্ধান্ত আমাদের নিতে হবে। কোনটা ক্রিমিনালে যাবে, কোনটা সিভিলে যাবে। এই দ্বন্দ্বের সমাধান না হলে আমরা বেশিদূর আগাতে পারবো না।’